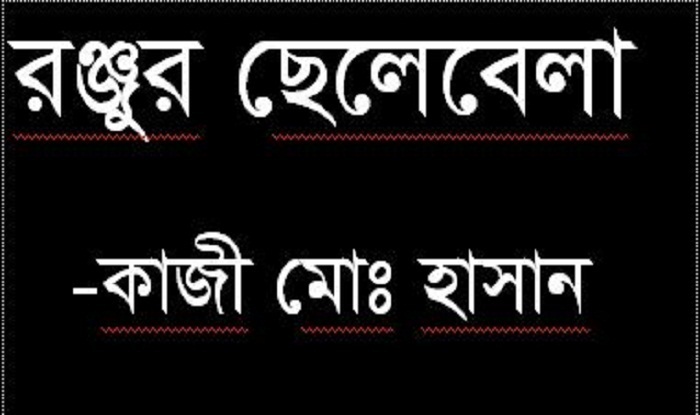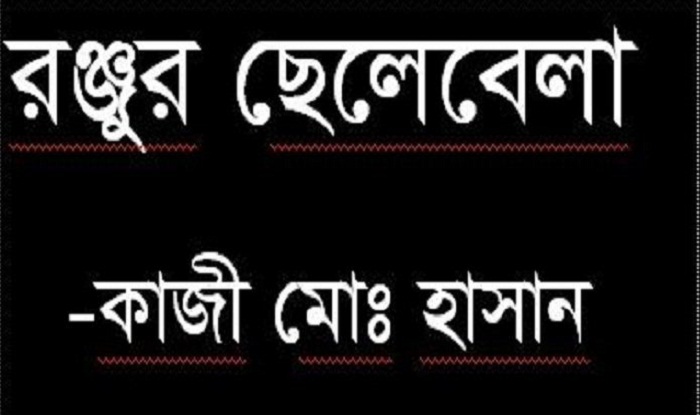-কাজী মোঃ হাসান
তিন দিন পর।
রঞ্জুদের বাড়িটা পূর্বমুখি। বাড়ির সামনে বড় উঠোন। তারপরেই গ্রাম্য রা¯তা। রাস্তাটা সরকার বাড়ির গুদারাঘাট থেকে নদীর তীর ঘেষে সোজা উচিতপুরা বাজার পর্যন্ত গেছে। এর পূর্ব পাশেই রঞ্জুদের ছাড়াবাড়ি, যেটা নদীতে গিয়ে ঠেকেছে। এখানেই রঞ্জুদের শান বাধানো ভাঙ্গা ঘাট।
আগে ছাড়াবাড়িটা যত বড় ছিলো এখন ততটা নেই। প্রতি বছরই নদীর দাপটে একটু একটু করে ভাঙ্গছে। আগে এখানে নাকি অনেক বড় বড় গাছপালা ছিলো, ছিলো খেলার মাঠ। সে সব রঞ্জুরা দেখেনি। শুধু শুনেছে। এখন তিনটা নারিকেল, দুইটা তাল এবং ছয়টা আম গাছ ছাড়া কিচ্ছু নেই। তন্মধ্যে পূর্ব-দক্ষিণ কোনার আম গাছের গোড়ার মাটি প্রায় অর্ধেকই হাওয়া। নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। মাটি না থাকায় শেকড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে হাতির দাঁতের মতো।
অনেক সময় রঞ্জুরা এই শেকড়গুলোর উপর বেসে বসে বরশি দিয়ে মাছ ধরে। মাছ বলতে দারখিনা, নলা, পুটি, মেনা, মলা, বাইল্যা এবং শোল মাছের পোনা- এইসব! তবে বেশীর ভাগই পুটি আর দারখিনা।
রঞ্জুর দাদু ছিলেন একজন নামকরা কবিরাজ। আশেপাশের দশ গ্রামে তাঁর মতো নামীদামী কবিরাজ কেউ ছিলেন না। কবিরাজী ছাড়াও তিনি মাদ্রাসায় অবৈতনিক ভাবে শিক্ষকতা করতেন। তার একটাই লক্ষ্য- দেশের মানুষকে শিক্ষিত করা।
মাদ্রাসায় মক্তব চলতো সকালে। দশটা থেকে বড়দের ক্লাশ শুরু। এ পর্বে কোরআন, হাদীস, ফেকাহ শাস্ত্রের পাশাপাশি বাংলা-ইংরাজিও পড়ানো হতো। তবে একটাই মুশকিল, মাদ্রাসায় প্রচুর ছাত্র থাকা সত্ত্বেও মান সম্পন্ন শিক্ষকের খুব অভাব। তাই দাদুর এই শিক্ষকতা করা।
এ মাদ্রাসারই মক্তব বিভাগের ছাত্র রঞ্জু। মাত্র কায়দা শিখছে।
একদিন মক্তব থেকে বেরিয়েই রঞ্জুরা মিলে ঠিক করে, আজ দুপুরে সাঁতার প্রতিযোগিতায় নামবে। সাঁতরে নদীটার এপার থেকে ওপারে যাবে। এ জন্য পুরস্কারেরও ব্যবস্থা আছে। প্রথম জন পাবে একটা চার নম্বর খাতা, দ্বিতীয় জন একটা কাঠ পেন্সিল, আর তৃতীয় জন দুই নম্বর খাতা একটা।
নির্দিষ্ট সময়ে সাঁকোর উপর এসে রিপোর্ট করে রঞ্জুরা। পানিতে নেমে সাঁতার দেয়ার প্রস্তুতিও শেষ। ঠিক সেই মুহূর্তে ভোজবাজির মতো মাটি ফুঁড়ে রমিজ কাকা এসে হাজির। রঞ্জুদের পানিতে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন তিনি-
– কিরে, কী করছিস তোরা?
– কিছু না কাকা, কিছু না। ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয় রিন্টু।
– কিছু না হলে পানিতে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? গোসল করে শিগগির উঠে আয়। চারিদিকে আজকাল যা জ্বর-জারি হচ্ছে—-! কথাটা বলেই তিনি সাঁকোর হাতলের উপর আয়েশ করে বসে সিগারেট ধরালেন। তারপর ডানে-বায়ে হেলে-দুলে মাথা ঝাঁকিয়ে হালকা ব্যায়াম করলেন একটুখানি।
বিপদ দেখে রঞ্জুরা একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। এর অর্থ- এখন কী করা যায়? ঘাড় নেড়ে সবাইকে উঠে যেতে আদেশ দেয় রিন্টু। এ ছাড়া উপায়ই বা কি? রমিজ কাকার সামনে সাঁতার দেয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। নির্ঘাত বিচার দেবেন হুজুরের কাছে।
আস্তে আস্তে সবাই যার যার মতো কয়েকটা ডুব দিয়ে উঠে আসে পানি থেকে। রমিজ কাকাকে আড়াল করে একটা ঘরের ওপাশে গিয়ে বসে পড়ে চুপচাপ। সবার চোখেমুখে প্রোগ্রাম মিস হওয়ার হতাশা। এবার অপেক্ষার পালা, কখন কাকা চলে যান।
রমিজ কাকার সিগারেট শেষ না হতেই আসেন তোতা কাকা। তিনিও রমিজ কাকার পাশে বসে গল্প শুরু করেন হাত নেড়ে নেড়ে। ফুচুর ফুচর করে রাজ্যের সব গল্প। রঞ্জুরা উঁকি দিয়ে দেখে- না, উঠার কোন নাম গন্ধ নেই। এদিকে, উঁকি-ঝুঁকি দিতে দিতে কখন যে বিকেল হয়ে গেছে, টেরই পায়নি তারা। শেষ পর্র্যন্ত সেদিনের মতো সাঁতারের পরিকল্পনা বাতিল করে বাড়ি ফিরে গেলো সবাই।
এর কিছুদিন পরের ঘটনা। দিনটা শুক্রবার। মক্তব বন্ধ। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকে। সূর্য একটু দেখা দিয়েই আবার চলে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে। এদিকে মাঠ-ঘাট ভিজে স্যাতস্যাতে। এ অবস্থায় দূরে কোথাও খেলতে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। খেলাও জমে না। তাই মক্তব থেকে ফিরে নাস্তা খেয়ে ঘরের বারান্দায় বসে মাটির উপর আঁকিঝুকি করছিলো রঞ্জু। হঠাৎ বাড়ির অন্যান্য বন্ধুদের উঠোনে চারা খেলতে দেখে নিজেও ছুটে গেলো সেখানে। কিন্তু পনেরো মিনিটের মধ্যেই সব শেষ। দাগে পারা পড়ায় ঝগড়ার শুরু। সুতরাং খেলা খতম!
কিছুক্ষণ গোলমালের পর আবার অন্য খেলায় সম্মত হয় তারা। এবার ডাংগুটি। প্রথমেই রঞ্জুর পালা। চারদিকে নজর রেখে ডাংগুটিটা ছুড়ে দিলো সে।কিন্তু গুটিটা লাফিয়ে ধরে ফেলে রিন্টু। কাজেই আউট। এবার রফিকের পালা। তারপর মিন্টুর।
এমন সময় দূর থেকে দাদুর কন্ঠ ভেসে আসে-
ঃ কই রে রঞ্জু, কোথায় গেলি?
ঃ এই যে দাদু, আমি এখানে। বলতে বলতে খেলা ফেলে ছুটে যায় দাদুর সামনে।
দাদু তাকে দেখেই বললেন-
ঃ হ্যারে রঞ্জু! পাঞ্জার ডালা কিনতে কান্দাপাড়া যাচ্ছি। যাবি আমার সাথে?
ঃ হ্যাঁ, যাবো! মনে মনে ভাবে, যাবো না মানে- একশ’ বার যাবো। নৌকায় চড়ে ঘুরে বেড়াবার এমন সুযোগ সহজে আসে না-কি?
দাদুর সঙ্গে যাওয়ার জন্য আগ বাড়িয়ে নৌকায় উঠে পড়ে। কান্দাপাড়ার পুরু গ্রামটা ঘুরে ছোট বড় মিলিয়ে পাঁচটা গাছ কিনলেন দাদু। কাঠুরিয়াকে ডেকে পরশুর মধ্যেই ডালা কেটে পাঞ্জা তৈরীর সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন।
বর্ষার দিনে যার যার সুযোগ মতো বিশেষ করে বাড়ির সামনের নদীর অংশে বাঁশের খুঁটি দিয়ে সীমানা চিহ্নিত করা হয়। তারপর গাছের ডালপালা ফেলে, কচুরী পানা, ঝরা ধান বা ধাম জড়ো করে অথবা অন্য কোন উপায়ে মাছের জন্য তৈরী করা হয় নিরাপদ জায়গা। এরই নাম পাঞ্জা বা ঘের। পানি কমে এলে অর্থাৎ ফাগুন-চৈত্র মাসে পাঞ্জার চারদিকে ফালার ঘের দিয়ে ঐ জায়গার মাছ ধরা হয়।
রঞ্জুদের পাঞ্জাটা অনেক বড়। এক সপ্তাহ পর থেকে পাঞ্জার খোঁপে খোঁপে চাঁই পাতা শুরু করলেন কাকা। তার সাথে বড় বড় বাঁশের চোঙ্গা। চিহ্ন রাখার জন্য সবকিছু পাতা হতো খুঁটির কাছাকাছি।
চোঙ্গাগুলো বরাগ বাঁশের তৈরী। বাঁশটা দু’ভাগ করে মাঝের ঘাটগুলো সরিয়ে আবার বেঁধে নিলেই চোঙ্গা তৈরী। দেখতে অনেকটা বর্তমানের ছয় ইঞ্চি ডায়া প্লাাষ্টিকের পাইপের মতো।
বাইম, শিং, মাগুড়- এসব মাছ নিরাপদ আশ্রয় ভেবে ঢুকে যেতো চোঙ্গার ভেতর। কয়েকদিন ঠিকই নিরাপদে কাটতো তাদের জীবন। তার পরই মহা বিপদ উপস্থিত। সুযোগ বুঝে কাকা চুঙ্গাটার দুই মুখ হাত দিয়ে বন্ধ করে আস্তে আস্তে ডাঙ্গায় তুলে আনলেই বিপদের চূড়ান্ত, ধরা পড়তো সব মাছ। কয়েকটা চোঙ্গা তুললেই ডুলা ভর্তি।
পাঞ্জা ফেলার এক মাস পরের কথা। একদিন দাদু রঞ্জুকে বেলালের চাচার কাছে পাঠালেন, তাদের ছাড়াবাড়ির নারিকেলগুলো পেড়ে দেয়ার জন্য। বেলালের চাচা নারিকেল গাছে উঠতে ওস্তাদ।
লাফাতে লাফাতে বেলালদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় রঞ্জু। তার উপর দায়িত্ব ছিলো- বেলালের চাচা কবে আসবেন, কখন আসবেন- সব জেনে আসা।
কথা মতো, শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষ করেই তিনি চলে আসেন রঞ্জুদের বাড়িতে। বরান্দায় বসে পান চিবুতে চিবুতে দাদুর সঙ্গে খোশগল্প করলেন কিছুক্ষণ। তার পর মালসামানা নিয়ে সোজা ছাড়াবাড়িতে। রঞ্জুরাও তার পিছু পিছু সেখানে গিয়ে উপস্থিত। তারা না গেলে নারিকেল কুড়াবে কে?
গাছে উঠার আগে কষে মালকোচা দিয়ে, কোমরে গামছা পেচিয়ে, রশি ছেনি ইত্যাদি রাখার ঝুড়িটা বেঁধে নিলেন কোমরে । হাতে থুতু ছিটিয়ে ভালো মতো ঘষে আঠা আঠা করে নিলেন হাতের তালু। সবশেষে পায়ের আঙ্গুলে রশি পেচিয়ে তরতর করে উঠে গেলেন নারিকেল গাছে।
বেলালের চাচা খুব গাগু লোক। মাথার ঠিক কাছাকাছি পৌঁছেই রশি দিয়ে বাঁশের লাঠিটা গাছের সাথে শক্ত করে বেঁধে সেটার উপর জুতসই করে বসে ছেনিটা তুলে নিলেন হাতে। এবার নারিকেলের ফাঁকে ফাঁকে সতর্কভাবে চোখ রেখে কি যেন খুঁজতে থাকেন মনযোগ দিয়ে। তারপর ছেনি দিয়ে কয়েকবার নারিকেল গাছের ডাউগ্যায় বাড়ি দিলেন জোরে জোরে। বলা তো যায় না- যদি গাছে কোন সাপটাপ থাকে। থাকলেও কোন অসুবিধা নেই, এতো আওয়াজের পর সাপ-বিচ্ছুর বাপও লুকিয়ে থাকতে পারবে না, বেড়িয়ে আসতে বাধ্য।
শুরু হয় নারকেল পাড়া। তিনি ছেনি দিয়ে নারিকেলের ছড়ায় কোপ দেন, আর ধুপধাপ করে মাটিতে পড়তে থাকে সেগুলো। সাথে সাথে রঞ্জুদের ব্যস্ততা বাড়ে। কাজ তো একটাই- নারিকেল কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করা। তার পরও সবার চোখেমুখে ঘাম চিকচিক করে। তাদের এই ব্যস্ততা দেখে ধমকে উঠলেন দাদু-
ঃ এই যে বাচ্চারা। থাম তোরা। শিগগির এদিকে আয়! এখন নারিকেল কুড়াবার দরকার নেই। পাড়া শেষ হলে তখন দেখে-শুনে সব একত্র করা যাবে। এভাবে কুড়াতে গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে! কিন্তু কে শুনে কার কথা। সুযোগ পেলেই দাদুর অলক্ষ্যে দৌড়ে যাচ্ছে তারা।
এভাবে একে একে দুইটা গাছের নারিকেল পাড়া শেষ। তৃতীয়টায় উঠলেন তিনি। এই গাছেরও দশ পনেরোটা পাড়া হয়ে গেছে। নতুন একটা থোকায় হাত দেয়ার আগে নারিকেল গাছের কয়েকটা ডাউগ্যা কাটছিলেন ছেনি দিয়ে। ডাউগ্যাগুলো বাতাসে ভেঙ্গে এমনিতেই পড়ো পড়ো অবস্থায় ঝুলেছিলো এলোমেলো ভাবে।
এই ফাঁকে মাটিতে ছড়ানো নারিকেলগুলো একত্র করছিলো রঞ্জুরা। ছেনির কোপের সাথে সাথে থর থর করে কাঁপছিলো গাছটা। হঠাৎ বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেয়ে একটা ঝুনা নারিকেল খসে যায় বোটা থেকে। আর সা করে সেটা নেমে আসে নীচের দিকে।
হঠাৎ সেদিকে চোখ যায় রঞ্জুর। মনে হয়, তীর বেগে তার দিকেই যেন আসছে নারিকেলটা। বাঁচার জন্য ভোঁ দৌড় দেয় সে। গন্ডির বাইরে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। নারিকেলটা ছুটে এসে প্রচন্ড জোরে আঘাত করে রঞ্জুর মাথায়। আঘাতটা সামলাতে পারে না সে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় মাঠের উপর। তার পর আর কিছুই মনে নেই।
জ্ঞান ফিরতেই দেখে, সে শুয়ে আছে খাটের উপর। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন দাদা-দাদী, জেঠা-জেঠি, ফুফু, চাচা-চাচী ও বন্ধু-বান্ধবরা। সবাই মিলে দোয়া-দরূদ পড়ছেন। চরম উৎকন্ঠা তাঁদের চোখে মুখে।
এ আঘাতটা রঞ্জুকে সহজে ছাড়লো না। বলা যায়, সেদিন থেকেই তার অসুস্থতা শুরু। খেলাধুলা, লেখাপড়া, হাটাচলা একদম বন্ধ। সারাক্ষণ ফ্লাট হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকার হুকুম। এছাড়া কোন উপায়ও নেই। উঠতে চাইলেও পারছে কই? মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে বারবার। এ ভাবে কদ্দিন যাবে, তা- আল্লাই জানেন!
দিন পনেরো পর। একটু হাটা-চলা করতে পারলেও দেখা দেয় আর এক ঝামেলা। কথা নেই, বার্তা নেই, ভয়ের কোন দৃশ্যেরও দেখা নেই, তারপরও ভয়ে হঠাৎ চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে রঞ্জু। আজকাল প্রায়ই ঘটছে ব্যাপারটা এবং সবার সামনেই।
এই তো সেদিন। উঠানে বসে ‘ওছা’ (বাঁশের তৈরী মাছ ধরার এক ধরণের অস্ত্র) ঠিক করছিলেন দাদু। দেখার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে সেদিকেই যাচ্ছিলো রঞ্জু। ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে সবে মাত্র উঠোনে পা দিয়েছে, হঠাৎ দেখে- একটা পাথর ঘুরতে ঘুরতে তীব্র গতিতে তার দিকেই ছুটে আসছে। সে যত সরে যেতে চাইছে, পাথরটাও তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে ছুটে যাচ্ছে পিছু পিছু। শুধু কী তাই, প্রথম দিকে পাথরটা থাকে খুব ছোট। আস্তে আস্তে সেটা বড় হয়ে প্রচ- শক্তিতে আঘাত করে রঞ্জুর উপর। তীব্র আর্তনাদ করে জ্ঞান হারায় সে। চিৎকার শুনে ছুটে আসেন বাড়ির সবাই। কিন্তু ততক্ষণে উঠোনে লুটিয়ে পড়ছে রঞ্জুর বেহুশ দেহটা।
বিষয়টা ভাবিয়ে তোলে সবাইকে। কারণ, তার বাপ-চাচারা চার ভাইয়ের মধ্যে তখনও সে-ই একমাত্র সন্তান। তা ছাড়া রঞ্জুর প্রতি সবার ভালোবাসাটা একটু বেশীই। তাই রোগ মুক্তির জন্য যে যা বলছে, যে যা দিচ্ছে, চোখ বন্ধ করে সেটাই করে যাচ্ছে তারা। আত্মীয় স্বজনেরাও সাহায্য-সহযোগিতা, উপদেশ এবং পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন সমান তালে। এক কথায়- চিকিৎসা এবং সেবা-যতেœর কোন ত্রুটি নেই।
রঞ্জুর দাদু তো আছেনই, এ ছাড়া অন্য কবিরাজও দেখানো হলো, অনেক ঔষধ খাওয়ানো হলো, কিন্তু কোন কিছুতেই কোন কাজ দিলো না। লোহা, তামা, রূপা, সোনা থেকে শুরু করে কত ধরনের তাবিজ যে তার গলায় উঠেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এসবের মধ্যে আছে চাড়া পড়া, চামরা পড়া, কানা পয়সা পড়া, সূতা পড়া। মাটি পড়াও বাদ যায়নি। দিনে দিনে রঞ্জুর গলার তাবিজের মালাটা বড় হতে হতে ঝুলে পড়েছে বুক পর্যন্ত।
আসলে, কি যে করা কিছুই মাথায় আসছে না কারোর। রঞ্জুর শরীর দিনকে দিন খারাপ থেকে খারাপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দাদু এত বড় কবিরাজ, তিনিও এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ।
অসুস্থতার খবর শুনে ছুটে এলেন আব্বু-আম্মু। আব্বু একজন ডাক্তার। দাদুর কবিরাজী এবং কিছু পারিবারিক কারণেই হয়তঃ ডাক্তার হতে উদ্বোদ্ধ হয়েছিলেন আব্বু। ন্যাশনাল কলেজ থেকে পাশ করে এখন প্রেকটিস করছেন। চেম্বার ও ফার্মেসী দিয়েছেন স্থানীয় থানা হেড কোয়ার্টার বাজারে।
পরীক্ষা নিরীক্ষার পর চিকিৎসাপত্র দিলেন আব্বু। তাও আজ তিন দিন। উন্নতির কোন লক্ষণ নেই। ফলে ভাবনাটা বেড়ে দিনকে দিন দুর্ভাবনায় পরিণত হলো হবার জন্য।
শেষ পর্যন্ত হাওয়া ও পরিবেশ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা। ঠিক হলো- আপাততঃ রঞ্জুর আব্বু যেখানে থাকেন, সেখানেই নিয়ে যাওয়া হবে রঞ্জুকে। অবস্থা বুঝে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।
এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করে রঞ্জু। দাদা-দাদীকে ছেড়ে কিছুতেই যাবে না সে। কিন্তু সে যেতে চাক বা না চাক, যেতে তাকে হবে- এটাই ফাইনাল। ঠিক হয়ে যায় যাওয়ার দিনক্ষণও।
(চলবে——-)
(‘রঞ্জুর ছেলেবেলা’ -থেকে)